শেষের কবিতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমিত চরিতে লেখকে স্বকীয় রচনাভঙ্গির সাথে সাধারণ সাহিত্যরীতিকে মুখ ও মুখোশের সাথে যে তুলনা করেছেন তা বোধ হয় সেই সময়ের জন্য চিন্তার খোরাক হয়ে উঠেছিল।
কিন্তু ঠিক তারপরই অযাচিত ভাবে খ্যাতিমান লেখককে অবজ্ঞা করা। অখ্যাত লেখকে গৌরবান্বিত করে তোলা। কিংবা কোন লেখকের লেখা না পড়ে ত্রুটিপূর্ণ, দোষযুক্ত অনুমাননির্ভর নেতিবাচক মন্তব্য করা। আবার সুহৃদ লেখকের সৃষ্টিকর্মকে অনন্য বলে অভিহিত করা শতবছর পূর্বেও ছিল। ভেবে অবাক হই। আজ এই সময়ে ঢাকার সাহিত্যলোকও সোশ্যাল মিডিয়া মুখহীন হয়ে, অমিতের মুখোশ পড়ে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে। ভেবে অবাক হই!
বিয়ে ও পাত্রী নির্বাচন সম্বন্ধে অমিত মানুষ হয়ে জন্মানো ও ব্যাক্তি হয়ে গড়ে উঠার যে সীমারেখা টেনে দেন, তা এক কথায় চিন্তাকর্ষক।
লেখক যখন নিজকেই চরিত্র হিসাবে আখ্যানকান্ডে আর্বিভূত হন, তবে সেটা আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গ হিসাবে নয় বরং গল্পের স্টাইল হিসাবে। তখন পাঠক হিসাবে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। অমিতের কবি ও কবিতার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি আলোচ্যবস্তু হিসাবে নিয়ে আসেন। এটি বোধহয় বাংলাদেশে প্রথম।
রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসগুলোতে স্থান হিসাবে যেভাবে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাকে অবলম্বন করেছেন তা চমৎকার লাগলো। বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পূর্ব থেকেই অখন্ড বাঙলাকে যেভাবে পুনঃপুন বাংলাদেশ নামে অভিহিত করেছেন, তাতে আমি বারংবার চমকে উঠাছি।
চোখের বালির মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারী আর নৌকাডুবির রমেশ-কমলা-হেমনলিনী-নলিনাক্ষ মতো শেষের কবিতায়ও রবিবাবু অমিত (অমিট)-লাবণ্য-কেতকী (কেটি)-শোভনলাল এর চতুরঙ্গ প্রণয়ের যুগল অদলবদলের ছাঁচের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এদিকটা আমায় বরাবরই উদাস করে তোলে। দেখা যাক পরবর্তী উপন্যাসে এমন পুনরাবৃত্তি হয় নাকি। তবে এ বিষয়টা একান্তই লেখকে নিজস্ব অধিকার। এখানে পাঠক, সমালোচক বা অন্যলেখকের জোরজবরদস্তি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।
পত্র কাব্য আর অলোক সংলাপের অবিশ্রাম নির্ঝরণীর জলধারায় কেমন আর্দ্র আর স্নিগ্ধ হয়ে ছিলাম। সত্তরের কোঠা ছুঁই ছুঁই বয়সে এমন প্রণয় উপন্যাস সৃষ্টি করা এক অলীক কর্ম।
প্রাচীন কালিদাস হতে মধ্য জয়দেব তার আধুনিক মধুসূদনের সৃষ্টিকে অমূল্যরূপে নিজ সৃষ্টিতে নিমন্তণ করে বাঙলা ভাষার ঐশ্বর্যকে যেন অকৃত্রিমতার প্রলেপ দিয়ে দিলেন।
অপরদিকে ইউরোপীয় ওয়র্ডসওয়র্থ ও আমেরিকান এমারসনের Transcendentalism যেন আখ্যানের বাক্যে অন্তঃস্থিত শূন্য রেখায় রেখায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। যেখানে প্রকৃতির অসীমতা আর অতীইন্দ্রীয়বাদের সাথে ব্যাক্তির অলক্ষ মিলন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।
শেষের কবিতায় অমিতকে লাবণ্যর শেষ কবিতায় যে অর্ঘ্য যে নৈবেদ্য সমর্পণ করেছে। তাতে মনে হলো, শেষ হয়েও হলো না শেষ।
"কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।"
📘শেষের কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯২৯।
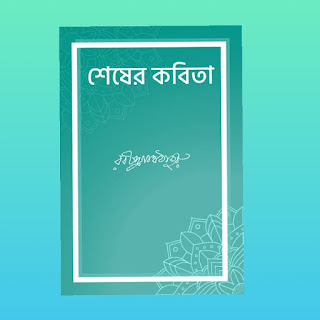


_-_Hap_Hadley_poster.jpg)
Comments
Post a Comment